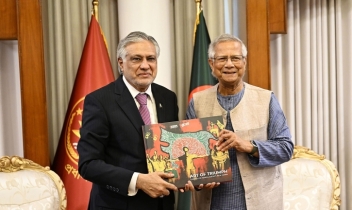প্রত্যাবাসন না আত্মীকরণ: রোহিঙ্গা সংকটের অবস্থা

প্রত্যাবাসন নাকি স্থানীয়ীকরণ: রোহিঙ্গা সংকটের দীর্ঘায়িত বাস্তবতা ও বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ
২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের সর্ববৃহৎ ঢল বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এরপর থেকে এই সমস্যাটি প্রায় আট বছর ধরে দীর্ঘায়িত শরণার্থী সংকটে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ নীতিনির্ধারকরা এখনও এ সিদ্ধান্তকে ‘চরম ভুল’ হিসাব করে থাকলেও মানবিক কারণে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি স্বাভাবিক ঘটনা।
রোহিঙ্গা সমস্যা অন্যান্য আন্তর্জাতিক শরণার্থী সমস্যার চেয়ে ভিন্ন। তারা কোনো যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পালায়নি, বরং একপক্ষীয় নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার। মিয়ানমারের কোনো সরকারই তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি, বরং নিধন ও বিতরণের নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে।
এই সংকটে ভারত, চীন ও রাশিয়ার নীরব ভূমিকা মিয়ানমারকে উৎসাহিত করেছে। শরণার্থীদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার দিক থেকে চাপ বাড়ায়, ফলে বাংলাদেশ সরকার তাদের ক্যাম্পের মধ্যেই সীমিত রাখতে বাধ্য হচ্ছে। তবে রোহিঙ্গাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যাম্পে কোনো দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ নেই।
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সন্ত্রাসী কার্যক্রম, চোরাকারবারি ও মাদক ব্যবসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানবিক সহায়তার প্রয়োজন বছরে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলার, যা এই আট বছরে প্রায় অর্ধেকে নেমেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় শরণার্থীদের স্থানীয়ভাবে আত্মীকরণের দিকে জোর দিচ্ছে, তবে বাংলাদেশের পক্ষে তা সম্ভব নয়।
একই সঙ্গে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা সংকট একটি চ্যালেঞ্জ। প্রত্যাবাসন ও তৃতীয় দেশে স্থানান্তরের সুযোগ সীমিত, তাই শূন্য স্থানীয় আত্মীকরণ নীতি কার্যকর রাখা হচ্ছে। ভাসানচরের মতো প্রকল্প এই চাপ কমানোর একটি উদাহরণ।
সরকার চীনের নেতৃত্বে দ্বিপক্ষীয় সমাধান এবং যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা—উভয় পথ বিবেচনা করছে, তবে জটিল ভূরাজনীতি ও সার্বভৌমত্বের কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। মিয়ানমার না চাইলে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ও কার্যকর করা সম্ভব নয়।
সর্বশেষ, রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই সমাধান এবং দেশের উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ধারাবাহিক, ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার প্রয়োজন। জাতীয় ঐকমত্য ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই সংকট থেকে মুক্তি সম্ভব নয়।