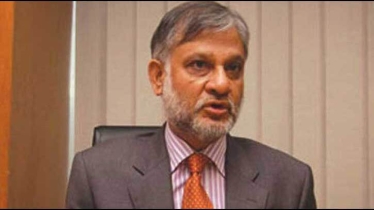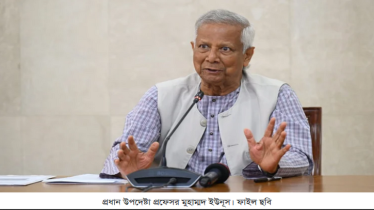বিদেশি বৃক্ষ: ‘লোভের’ রোপণে বনের প্রাণ যায় যায়

খাগড়াছড়ির একটি বনে এভাবেই একরের পর একর সেগুন গাছ রোপণ করা হয়েছে।
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জীববৈচিত্র্যের আধার হিসেবে গড়ে উঠা প্রাকৃতিক বনকে ‘অনুৎপাদনশীল’ আখ্যা দিয়ে ‘অর্থকরী’ বন সৃজনের নামে ‘পরিবেশ-বিধ্বংসী’ গাছ লাগিয়ে খোদ বনবিভাগই যেন বনের ‘পায়ে কুড়াল মেরে’ বসেছে।
সেগুন, রাবার, অ্যাকাশিয়া, ইউক্যালিপটাসের মতো বিদেশি গাছের আগ্রাসনে যখন মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে, পাহাড়ের ঝিরি-ঝর্ণার জল উধাও হয়ে যাচ্ছে, বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে- তখন বনবিভাগের ‘বোধদয়’ হয়েছে মনোকালকালচারের বিপরীতে দেশীয় গাছ রোপণ বা মিশ্র বাগান করে বনের ‘ভারসাম্য’ রক্ষার।
অথচ বনকে ‘অর্থকরী’ করার জন্য বাণিজ্যিকভাবে শত শত একর জমিতে এসব ‘পরিবেশ-বিধ্বংসী’ গাছ রোপণ কিংবা মনোকালচার-ভিত্তিক বাগানের অনুমতি এখনও অব্যাহত আছে।
এই ধারা থেকে বেরিয়ে না এলে আগামী দিনেও বন ও পরিবেশের জন্য সুখবর নেই বলে মনে করছেন পরিবেশ সংশ্লিষ্টরা।
খাগড়াছড়ির বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মো. ফরিদ মিঞা বলছিলেন, “একটা সময় বনবিভাগের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মূল্যবান কাঠ উৎপাদন করা। আলুটিলায় ছয় হাজার ২০০ একরের বেশি ভূমিজুড়ে যে সংরক্ষিত বন রয়েছে, তার পুরোটাই সেগুন বাগান।
“এখন সে দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টেছে। কারণ সেগুনের মত গাছের এত বেশি নেতিবাচক প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা এখন মিশ্র বন গড়ে তোলার দিকে নজর দিচ্ছি।”
কিন্তু অর্থমূল্যের বিবেচনায় সেগুন যে এখনো ব্যবসায়ীদের পছন্দের শীর্ষে, সে কথাও স্বীকার করছেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা।
ঔপনিবেশিক মনে ‘অর্থকরী’ বন
সেগুন, রাবার, অ্যাকাশিয়া, ইউক্যালিপটাসের মত বৃক্ষ দেশীয় নয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় বা এদেশের বনে এসব বৃক্ষ কখনও প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়নি।
১৮৭২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকরা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বনকে ‘অনুৎপাদনশীল বন’ আখ্যায়িত করে। মূলত তার পর থেকেই দেশে বনকে ‘অর্থকরী’ করার দিকে নজর দেয় কর্তৃপক্ষ।
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট-সেড প্রকাশিত বইয়ে ‘বন, বনবিনাশ এবং বনভূমিতে বিদেশি প্রজাতির আগ্রাসন’ শীর্ষক প্রবন্ধে ফিলিপ গাইন লিখেছেন, “প্রাকৃতিক বন কেটে সেখানে তাদের ঘর-বাড়ি বানানোর জন্য মূল্যবান কাঠ উৎপাদনের নিমিত্তে সেগুন গাছ লাগানো শুরু হয়। বার্মা থেকে আনা সেগুনের বীজ লাগানো হয় রাঙামাটির কাপ্তাইয়ের সীতা পাহাড়ে।
“পরবর্তীতে পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সেগুন মনোকালচারের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করে। সেগুন দেশের সর্বত্র মূল্যাবান কাঠ। সরকারি বনভূমি ছাড়াও ব্যক্তি মালিকানাধীন বনে সেগুনের ব্যাপক প্রসার ঘটে।”
এরই ধারাবাহিকতায় গত শতাব্দীর আশির দশকে পাহাড়ে ব্যাপক হারে রাবার বাগান, ইউক্যালিপটাস চাষের অনুমতি দেওয়া হয়। যদিও এ শতাব্দীর গোড়ায় এসে এসব গাছের অপকারিতা সম্পর্কে অবগত হয় বনবিভাগ। এসব গাছ যে সবসময় অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়েছে, তাও নয়।
বান্দরবানের তুলনায় খাগড়াছড়ি, রাঙামাটিতে সেগুনের আধিক্য বেশি। প্রাকৃতিক বন উজাড়ের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে সেগুন। কাঠ মূল্যবান হওয়ায় সেগুনের বাজার ছড়িয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম ও ঢাকায়। বর্তমানে সেগুন উৎপাদন ও বিপণনের সঙ্গে অনেক মানুষের জীবন ও জীবিকা জড়িত। বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় বনজ শিল্পের সিংহভাগ দখল করে আছে সেগুন।
তবে সেগুনের নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে বনবিভাগও উদ্বিগ্ন। যদিও খাগড়াছড়িতে সেগুন বাগান কী পরিমাণ রয়েছে বনবিভাগের কাছে সে তথ্য নেই।
খাগড়াছড়ির বিভাগীয় বনকর্মকর্তা মো. ফরিদ মিঞা বলেন, “পাহাড়ে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য না থাকলে পরিবেশে উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সেগুনের কারণে পাহাড়ে মাটিক্ষয় বাড়ছে। সে মাটি ঝিরি, ছড়া হয়ে নদীতে গিয়ে পড়ছে। প্রাকৃতিক বনে মাটি সবসময় শীতল থাকে। সেখানে বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ, লতাগুল্মে আচ্ছাদিত থাকায় মাটি নির্মল থাকে, পানির উৎস স্বাভাবিক থাকে এবং মাটির ক্ষয় থেকে রক্ষা পায়।”
জল-জীবের হুমকি
খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়ক লাগায়ো পাহাড়ি গ্রামের নয় মাইলের নিচ দিয়ে বয়ে গেছে বেতছড়ি ছড়া। পাড়ার মধ্য দিয়ে খানিকটা পথ হেঁটে ছড়ায় যাওয়া যায়। বর্ষাকালে ছড়াটিতে পানি থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে ছড়ার পানি শুকিয়ে যায়।
স্থানীয় বাসিন্দা ও বনবিভাগের কর্মীদের ভাষ্য, এলাকায় অনেকগুলো সেগুন বাগান থাকায় এই অবস্থা হয়েছে।
সেগুন গাছ অন্য গাছের চেয়ে অনেক বেশি পানি শোষণ করে। ফলে এর আশপাশের মাটিতে জল কমে যায়। এ কারণেই সেগুনের বাগানে আর অন্য কোনো গাছ খুব একটা জন্মে না। তবে ক্ষতির মাত্রা কতটা ব্যাপক, সে বিষয়ে গবেষণা খুব বেশি হয়নি।
নয় মাইল এলাকার বাসিন্দা ও মেরুং ইউনিয়নের সাবেক সদস্য গণেশ ত্রিপুরা ত্রিপুরা বলেন, “আগে ছড়ায় পানি থাকত। এখন প্রাকৃতিক বন নেই। দুই পাশের পাহাড়ে প্রচুর সেগুন বাগান। সেগুন গাছ পানি শোষণ করে বেশি। এ কারণে ছড়া বা ঝিরি শুকিয়ে যায়।
“এখানে শুষ্ক মৌসুমে পানি নেই বললেই চলে। ছড়াগুলো মাইনী নদীতে গিয়ে পড়েছে। ছড়াগুলোতে পানির প্রবাহ কমায় নদীতেও পানি কমে যায়।”
খাগড়াছড়ির জেলার সংরক্ষিত বনের একটি বড় অংশ রাঙামাটির পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বনবিভাগের আত্ততাধীন। সেখানকার বিভাগীয় কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম প্রাকৃতিক বন থেকে সৃষ্ট মাইনি ও কাচালং নদীর উদাহরণ দিয়েছেন।
তিনি বলছিলেন, “দীঘিনালার নাড়াইছড়ি রেঞ্জের আওতাধীন সংরক্ষিত বনের আয়তন প্রায় ৪২ হাজার হেক্টর। মাইনী ও কাচালং নদী তো এই বন থেকে সৃষ্টি হয়েছে। প্রাকৃতিক বন থাকায় দুটো নদীতে শুষ্ক মৌসুমে এখনো পানির প্রবাহ রয়েছে। সংলগ্ন ছড়াগুলোতেও পানি থাকে।
সেগুন বাগানের আশপাশের যে ঝিরি, সেগুলোতে পানি থাকে না বলে জানালেন রেজাউল করিম।
তিনি বলেন, “২০০০ সাল থেকে বনবিভাগ সেগুন রোপণ বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর থেকে অফিসিয়ালি পার্বত্য এলাকায় আর সেগুন রোপণ করা হয়নি। কিন্ত ব্যক্তি উদ্যোগে প্রচুর সেগুন বাগান গড়ে উঠেছে। সেগুন মাটিকে অ্যাসিডিক করে তোলে।”
ভুল বুঝতে পেরেও ভুলে থাকা
সেগুনের পাশাপাশি পার্বত্য এলাকায় রাবার চাষ প্রকল্পও প্রাকৃতিক বনের সর্বনাশ করেছে। বিগত শতাব্দীর আশির দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ‘উঁচু ভূমি বন্দোবস্তকরণ রাবার বাগান প্রকল্প’ এর মাধ্যমে রাবার চাষ শুরু হয়।
এর আওতায় খাগড়াছড়িতে ২০ হাজার একরের বেশি জমিতে রাবার চাষ শুরু হয়। মূলত পাহাড়ি বন ধ্বংস করে রাবার চাষ করা হয়।
খাগড়াছড়ির দীঘিনালা, মাটিরাঙা, সদর, পানছড়ি, গুইমারা, রামগড়সহ বিভিন্ন উপজেলায় রাবার প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রকল্প নেওয়া হলেও দীর্ঘদিন পর রাবার অলাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে প্রমাণিত হয় বলে স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশবিদরা বলছেন।
এ কারণে অনেক বাগান থেকে রাবার গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। রাবারের বদলে গড়ে তোলা হচ্ছে ফলদ বাগান।
তবে এখনও প্রচুর পরিমাণে সেগুনের চাষ হচ্ছে বলে জানালেন খাগড়াছড়ির বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘জাবারং’ এর নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা।
তিনি বলেন, “পাহাড়ে সেগুনের বিস্তার ঘটিয়েছে বনবিভাগ। সেগুনের দাম বেশি হওয়ায় এটি এখন পারিবারিকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে। যেদিকেই তাকান সেগুন বাগানের আধিক্য।
“বিদেশি প্রজাতির বৃক্ষের মনোকালচারের কারণে বন স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠতে পারে না। পরিবেশের ভারসাম্য রাখতে হবে দীর্ঘমেয়াদে বিকল্প চিন্তা করতে হবে। দেশীয় প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ বা মিশ্র বনায়ন করতে হবে।”
প্রায় একই কথা বলছিলেন খাগড়াছড়ির পরিবেশ সংরক্ষণবাদী সংগঠন পিটাছড়া বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উদ্যোগের মাহফুজ রাসেল।
“পাম, সেগুন মাটির উপর অনেক চাপ সৃষ্টি করে। মাটি রুক্ষ হয়, ক্ষয় হয়। সেগুন প্রচুর পানি শোষণ করে। এখন পার্বত্য এলাকায় হাজার হাজার একর জমিতে কাসাভা চাষ হয়। কাসাভা চাষের কারণে মাটি ক্ষয়, পাহাড় ধসে। পাহাড়ের ক্ষয়ে যাওয়া মাটি ছড়া বা ঝিরিতে যায়। বিদেশি প্রজাতির গাছ আমাদের পরিবেশের জন্য উপযোগী নয়। এ কারণে আমাদের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে।’
মনোকালচারের বিকল্প ভাবনা
উনিশ শতকের শেষ দিকে ‘অর্থকরী’ বৃক্ষ আসার আগে পাহাড় ঘিরে ছিল মূলত প্রাকৃতিক বন। এসব বন ছিল পাহাড়ে বসবাসকারী সব প্রাণ-প্রজাতির আধার। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে পাহাড় থেকে প্রাকৃতিক বন নিঃশেষ হয়েছে। প্রাকৃতিক বন কমে বেড়েছে মনোকালচারভিত্তিক চাষ। প্রাকৃতিক বন নিঃশেষ হওয়ায় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে।
এখন আবার প্রাকৃতিক বন ফিরিয়ে আনা এবং মিশ্র বাগান গড়ায় উৎসাহ দিচ্ছে বনবিভাগ।
খাগড়াছড়ির বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ফরিদ মিঞা বলেন, “পার্বত্য এলাকায় এভারগ্রিন প্রজাতির প্রচুর গাছ রোপণ করা উচিত। আগের রোপণ করা সেগুন বা যেসব প্রজাতির বৃক্ষ প্রকৃতি রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে না সেসব প্রজাতির বৃক্ষ ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে। বনবিভাগ এখন সেই লক্ষ্যে কাজ করছে যাতে স্থানীয় জনগণ উদ্ধুদ্ধ হয়।”
পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বনবিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, “সেগুনের বিকল্প হিসেবে এখন মূল্যবান গামারি, স্বর্ণচাপা বা চম্পাফুল রোপণ করা যেতে পারে। এসব গাছের বাজার মূল্য সেগুনের কাছাকাছি। মনোকালচার না করে যদি মিশ্র বাগান করা যায় সেক্ষেত্রে বন অনেকটায় পুনরুজ্জীবত হবে। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রাকৃতিক বনের বিকল্প কিছুই নেই।”
একই কথা বলছিলেন খাগড়াছড়ির পরিবেশবাদী সংগঠন বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন সোসাইটি অব সিএইচটির সংগঠক সবুজ চাকমা।
তিনি বলছিলেন, “মানুষ এখন অভিজ্ঞতার নিরিখে সেগুনের পরিবর্তে ফলদ বাগান গড়ে তুলেছে। এটি তুলনামূলক ভালো। এ ছাড়া স্বর্ণচাপা সেগুনের বিকল্প হতে পারে। এটি পাখি ও জীব-বৈচিত্র্যবান্ধব গাছ। প্রাপ্তবয়স্ক স্বর্ণচাপার মূল্য সেগুনের কাছাকাছি।
“আমাদের সংগঠন প্ল্যানটেশন ফর নেচারের পক্ষ থেকে প্রায় ৭৭ হাজার স্বর্ণচাপার চারা বিভিন্ন বিহার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন বনে দেওয়া হয়েছে। সচেতনতা তৈরি করতে হবে। সেগুনের বিকল্প বের করতে হবে। যাতে মানুষ প্রকৃতিবান্ধব গাছ রোপণ করবে এবং বাণিজ্যিক মূল্যও পাবে।”
নেই গবেষণা-তথ্য
পরিবেশ বিনাশী গাছ নিয়ে নানা নেতিবাচক কথা বলা হলেও এ নিয়ে বিশেষ কোনো গবেষণা ও তথ্য বনবিভাগ বা ব্যক্তি পর্যায়ে নেই। ফলে প্রকৃতপক্ষে সেগুন বা এই জাতীয় বৃক্ষ অন্যান্য গাছ থেকে কী কী কারণে বিধ্বংসী সেই বিষয়ে জ্ঞানের অভাব রয়েছে।
বনকর্মকর্তা রেজাউল করিম স্পষ্ট করেই বললেন, “আসলে একটি সেগুন গাছ কী পরিমাণ পানি শোষণ করে সে তথ্য আমাদের নেই। এটি নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি।”
বনের পাখি সেগুন গাছে বাসা বাঁধে না। এর মূল কারণ সেগুনের শাখার গঠন। সেগুনের শাখা এত বেশি সরু যে পাখি বাসা তৈরি করার মত উপযোগী নয়।
শুষ্ক মৌসুমে সেগুন বনে আগাছা পরিষ্কার করার জন্য আগুন দেওয়া হয়। সেগুন গাছের নিচে লতাগুল্ম কিছুই হয় না। তাতে পুরো পাহাড়টা ন্যাড়া থাকে বলে মন্তব্য করলেন রেজাউল করিম।
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিউটের সয়েল সার্ভে অ্যান্ড ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মামুনুর রহমানও সেগুন নিয়ে দেশে কোনো গবেষণা না থাকার কথা বললেন।
ঢাকা বিশ্বদবিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিন বলেন, “সেগুন গাছ বেশি পানি শোষণ করে কি-না এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। তবে এই গাছের পাতা যেহেতু বড়, যেহেতু বিদেশি, ওদের প্রকৃতি একটু আগ্রাসী। এদের তলায় অন্য গাছ হয় না। প্রকৃতিগত কারণেই অন্য গাছ এরা খেয়ে ফেলে।”
সেগুন গাছে কেন পোকামাকড় বা পাখি বাসা বাঁধে না–এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “বাসা বাঁধার জন্য গাছের গঠনশৈলীও আলাদা হওয়া লাগে। যেখানে সে খড়কুঁটো নিয়ে রাখতে পারবে। সেগুন গাছের যে গঠনশৈলী, সেখানে সে ধরনের সিস্টেম নেই। একটা আম গাছের গঠনশৈলী আর সেগুন গাছের গঠনশৈলী এক না তো। মূলত গঠনশৈলীর জন্যই এসব গাছে বাসা বাঁধে না।”